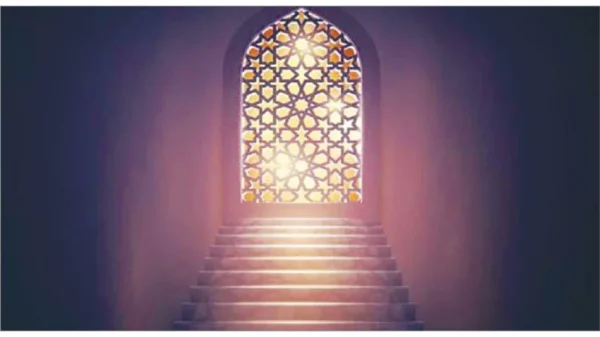বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৫৯ পূর্বাহ্ন
দেশ ভাগে ভাষার দ্বন্দ্ব ও ভূমিকা

মযহারুল ইসলাম বাবলা :
ভারতের মানুষের মাতৃভাষা কয়েকশ। এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪১৫টি। এই ৪১৫টি ভাষার উপভাষার সংখ্যা ১৫৭৬টি (১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে)। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ২৯টি কথ্যভাষায় ১০ লাখ মানুষ কথা বলে। ১২২টি কথ্যভাষা ১০ হাজার মানুষের মুখের ভাষা। এ ছাড়া অজস্র উপভাষা রয়েছে, যেগুলোর লিপি নেই। সেসব ভাষার অস্তিত্ব টিকে আছে মানুষের মুখে মুখে। বর্তমান ভারতের রাজ্যগুলোর ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। একই রাজ্যের একাধিক ভাষা যেমন রয়েছে, তেমনি একই ভাষা অপরাপর রাজ্যেও প্রচলিত আছে। ভারতের প্রাদেশিক সরকারি স্বীকৃত ভাষা (অসমীয়া, বাংলা, বোড়ো, ডোগরি, গুজরাটি, হিন্দি, কন্নড়, কাশ্মীরি, কোঙ্কনী, মৈথলী, মলয়ালম, মৈত্রৈ (মণিপুরি), মারাঠি, নেপালি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, সংস্কৃত, সাঁওতাল, তামিল, তেলেগু, উর্দু, মিজো ও কোকোবরক। ইংরেজি ভাষাও অনেক প্রদেশের সরকারি ভাষার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, যেমন অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও চণ্ডীগড়। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের তালিকাই প্রমাণ করে অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার মতো হিন্দিও প্রাদেশিক ভাষা। অনেক প্রদেশের সহকারী সরকারি ভাষা হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি, বাংলা, মারাঠি, পাঞ্জাবি, [খাসি, গারো, ভুটিয়া, গুরং, লেপচা, লিম্বু, মাঙার, মুখিয়া, নেওরি, রাজ, শেরপা, তমাং ইত্যাদি সিকিম প্রদেশের সহকারী সরকারি ভাষা।
প্রশ্ন থাকে বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতে প্রাদেশিক হিন্দি ভাষা কেন সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পেছনে ফিরে যেতে হবে। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি এক রাষ্ট্রের সুবিধায় ভারতে বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তার-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। ব্রিটিশদের মুৎসুদ্দি রূপে নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুযোগও হাতাতে পেরেছিল। তাদের মনস্কামনা পূরণে অন্তরায় ছিল ভাষার বিভক্তি। ব্রিটিশ ভারতেই ভারতীয় বুর্জোয়ারা স্বীয় স্বার্থে এককেন্দ্রিক শাসনের পাশাপাশি এক ভাষা ও এক জাতির আওয়াজ তুলেছিল। জাতি হিসেবে ভারতীয় এবং ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছিল তারা হিন্দি ভাষা-দেবনাগরী লিপি। নিজেদের কায়েমি স্বার্থে হিন্দি ভাষাকে ভারতের সমগ্র জাতিসত্তার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ফন্দি এঁটেছিল; অপরাপর ভাষা-সংস্কৃতি, স্বাজাত্যবোধকে বিলীন করে দেওয়ার মতলবে। ব্রিটিশ ভারতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সুবিধা ভোগ সম্ভব হলেও, তাদের পক্ষে হিন্দি ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষায় পরিণত করা সম্ভব হয়নি।
১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে এসে গান্ধী ভারতজুড়ে ভ্রমণ করেন। তখনই তিনি দেখতে পান ভারতীয় মাড়োয়ারি পুঁজিপতিরা গো-রক্ষা এবং হিন্দি ভাষা প্রচলনে নানান পন্থায় মদদ জুগিয়ে যাচ্ছে। গান্ধী সহসাই পুঁজিপতিদের পক্ষে সেই প্রচারাভিযানে যুক্ত হয়ে যান। অর্থাৎ গো-রক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি হিন্দি ভাষাকে সমগ্র জাতিসত্তার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বুর্জোয়া শ্রেণির আকাক্সক্ষা বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এই তৎপরতার মধ্য দিয়েই ভারতে গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে ‘সর্বভারতীয় এক ভাষা ও একলিপি সম্মেলন’ গান্ধীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে হিন্দি ভাষা প্রচারে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের উপকমিটির সভাপতি হয়েছিলেন গান্ধী। ভারতীয় মাড়োয়ারি পুঁজিপতিদের অর্থের জোগানে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু ন্যাশনাল কলেজে ১৯২০ সালের জুলাইয়ে গান্ধী বলেছিলেন, ‘হিন্দিই হবে সমগ্র ভারতের ভাষা এবং সেজন্য হিন্দি শেখা অন্যসব প্রদেশের কর্তব্য।’ গান্ধী প্রকাশ্যে বলে বেড়াতেন, ‘অহিন্দিভাষীদের হিন্দি শেখা হচ্ছে ধর্ম।’ ভারতীয়দের ধর্মীয় অনুভূতিতে হিন্দি ভাষা বিস্তারে ধর্মকে পর্যন্ত ব্যবহার করতে চেয়েছেন। হিন্দি ভাষাকে ধর্মীয় পর্যায়ভুক্ত করতেও দ্বিধা করেননি গান্ধী। গান্ধী লিখেছিলেন, ‘এলাহাবাদের হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে ১৮ মাসব্যাপী মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে হিন্দি ভাষার প্রচার খুব জোরালোভাবেই চলছে।’ হিন্দি ভাষাকে সমগ্র জাতিসত্তার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মাড়োয়ারি পুঁজিপতিদের অর্থানুকূল্যের বিষয়টিও স্বীকার করে গান্ধী বলেছিলেন, ‘হিন্দি প্রচারের কাজ ভারতের এই রাজতুল্য বণিকশ্রেণির বিশেষত্ব।’
১৯২১ সালে এক চিঠিতে গান্ধী মাড়োয়ারি পুঁজিপতিদের উদ্দেশে লিখেছিলেন, ‘ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর থেকেই আমি আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছি। আমার কাজে আপনারা প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। হিন্দি প্রচারের আন্দোলনকে আপনারা কার্যকরভাবে সমর্থন দিয়েছেন।’ গান্ধীর হিন্দি ভাষা প্রচারাভিযানে মাড়োয়ারিদের পাশাপাশি গুজরাটি, পার্শি বণিকশ্রেণিও আর্থিক সহায়তা প্রদানে পিছিয়ে ছিল না। বাংলা ও আসাম প্রদেশে হিন্দি প্রচারাভিযানে ১৯২৮ সালে হিন্দুত্ববাদী বুর্জোয়া ধনশ্যামদাস বিড়লাকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে কলকাতায় হিন্দি প্রচারের এক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে হিন্দি ভাষাকে জাতীয় ভাষায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজেন্দ্র প্রসাদকে সভাপতি করে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে ‘রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি’ গঠিত হয়। পরে স্বয়ং রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখেছিলেন, ‘এর নীতি স্বয়ং গান্ধীজি নির্ধারণ করেছিলেন এবং আমাদের শিল্পপতি বন্ধুরা অর্থের জোগান দিতেন।’
হিন্দি ভাষা ও দেবনাগরী লিপি সমগ্র ভারতীয়দের ওপর চাপানোর এই উদ্যোগে উত্তর প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। উর্দুভাষী মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চারে তারা উপলব্ধি করে হিন্দির দৌরাত্ম্যে তাদের উর্দু ভাষা-সংস্কৃতির বিলোপ ঘটবে। ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে লক্ষেèৗতে মুসলিম লীগ অধিবেশনে সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের জাতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার তীব্র নিন্দা জানায়।
১৯২৭ সালের জুলাইয়ে গান্ধী লিখেছিলেন, ‘সব ভারতীয় ভাষার একটি লিপি হওয়া উচিত এবং শুধু দেবনাগরীই হতে পারে সেই লিপি।’ গান্ধী বলেছেন, ‘হিন্দু-মুসলিম উন্মত্ততার জন্য সম্পূর্ণ সংস্কারের পক্ষে বাধা আছে। তবে এর আগে হিন্দু ভারতকে বুঝতে হবে যে, যেসব ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত তাদের লিপিগুলো, যেমন বাংলা, গুরুমুখী, সিন্ধি, ওড়িয়া, গুজরাটি, তেলেগু, তামিল, কন্নড়, মলয়ালম ইত্যাদি ভাষার লিপিকে বর্জন করে সে স্থলে থাকবে শুধুই দেবনাগরী লিপি। এর ফলে হিন্দু ভারত সংহত ও বলিষ্ঠ হবে।’ গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছেন পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান এবং অন্য সবাই উর্দু জানে (উর্দু ভাষার লিপি ফার্সি)। ধর্মের ভিত্তিতে ভাষার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন গান্ধী। পাঞ্জাবি হিন্দুরা দেবনাগরী লিপি গ্রহণ করবে এবং মুসলিমরা ফার্সি লিপি। একইভাবে বাঙালি হিন্দুর লিপি হবে দেবনাগরী এবং বাঙালি মুসলমানের লিপি হবে বাংলা অথবা ফার্সি। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরোধকে ভাষা ও লিপির ভেতরে টেনে আনেন স্বয়ং গান্ধী। ব্রিটিশদের বিভক্তীকরণের চক্রান্তের নীতি অনুসরণ কি ভাষার প্রশ্নে গান্ধী করেননি? হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভক্তি ব্রিটিশরা করেছিল তাদের শোষণ প্রক্রিয়া এবং দখলদারিত্ব স্থায়ী করার লক্ষ্যে। গান্ধীও হিন্দি ভাষা ও দেবনাগরী লিপির পক্ষে সম্প্রদায়গত বিভাজনের নীতি অনুসরণ করে সেই বিভাজনকেই সামনে নিয়ে এসেছিলেন।
হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক বিভাজন-বিভক্তি ব্রিটিশদের সৃষ্ট। সাম্প্রদায়িক বিভাজন নতুন মাত্রা পেয়েছিল গান্ধীর হিন্দি ভাষা ও দেবনাগরী লিপির জাতীয় ভাষা ও লিপির আন্দোলন অভিযানে। এতে দ্রুতই মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মুসলমানদের বিরোধিতার মুখে গান্ধী-নেহরুর মত পরিবর্তন করলেও; উর্দুভাষী মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দি-উর্দু ভাষা বিতর্কে সরব হয়ে ওঠে এবং ভাষা নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধেরও সূচনা ঘটে। ১৯৩৭ সালের জুলাইয়ে কংগ্রেস সভাপতি নেহরু বলেন, ‘অবশ্যই হিন্দি অথবা হিন্দুস্তানি হচ্ছে জাতীয় ভাষা এবং হওয়া উচিতও। লিপি সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা দরকার যে, হিন্দি ও উর্দু দুই লিপিই সহাবস্থান করা উচিত।… এই বিতর্ক বন্ধ করার জন্য ভালো হবে যদি আমরা কথ্যভাষাকে হিন্দুস্তানি এবং লিপিকে হিন্দি অথবা উর্দু আখ্যা দিই। ইউরোপের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর হিন্দিতে অনুবাদ হওয়া একান্ত দরকার।’ নেহরুর বক্তব্যটির সারকথা হচ্ছে, লিখিত ভাষা হিন্দিই হবে ভারতের জাতীয় ভাষা। সেটা দেবনাগরী কিংবা উর্দু দুই লিপিতেই লিখিত হতে পারে। ‘ভাষাপ্রশ্ন’ গ্রন্থে নেহরু লিখেছিলেন, ‘একমাত্র হিন্দুস্তানিই সমগ্র ভারতের ভাষা হতে পারে।’ লিপির ক্ষেত্রে দেবনাগরী এবং উর্দু লিপির কথাও মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষোভ প্রশমনে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।
গান্ধী মুসলমানদের বিরোধিতার মুখে হিন্দুস্তানির অনুরাগী হয়ে সেই লক্ষ্যে ১৯৪২ সালে ‘হিন্দুস্তানি প্রচার সভা’ সংগঠন গড়ে তোলেন। উত্তর ভারতে কথ্যভাষা রূপে হিন্দুস্তানি ভাষা ছিল বটে। তবে সেটি হিন্দি ও উর্দুর সংমিশ্রণে। লিপি না থাকায় লিখিত ভাষারূপে হিন্দুস্তানি ভাষার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের আগে ভারতের সংবিধান সভায় গান্ধী প্রস্তাব করেছিলেন, তারাই সংবিধান সভার সদস্য হতে পারবেন যারা হিন্দি ভাষার সঙ্গে পরিচিত। গান্ধী আরও দাবি করেন, ভারতের সংবিধান হিন্দুস্তানি ভাষায় লিখিত হতে হবে। মৃত্যুর আগে গান্ধী বলেছিলেন, ‘তার যদি ক্ষমতা থাকত তবে তিনি তাদেরই কংগ্রেসের সদস্য করতেন যারা হিন্দুস্তানি ভাষা জানেন।’ ১৯৪৭ সালে গান্ধী হিন্দুস্তানি ভাষাকে সমগ্র এশিয়ার ভাষায় পরিণত করার দিবা-স্বপ্নও দেখেছিলেন। মুসলিম বিরোধিতায় গান্ধী-নেহরুরা ভারতের জাতীয় ভাষা হিন্দির পরিবর্তে হিন্দুস্তানি কথ্য ভাষার প্রচারণা ছিল প্রতারণার কৌশল। উদ্দেশ্য ছিল দেবনাগরী লিপির বাতাবরণে হিন্দি ভাষাকেই সমগ্র জাতিসত্তার স্কন্ধে চাপানোর। বাস্তবতা হচ্ছে হিন্দুস্তানি ভাষা প্রকৃতই কথ্য ভাষা। সে ভাষার ছিল না লিপি। ছিল না সাহিত্য। সেটি শুধুই আঞ্চলিক কথ্যভাষা মাত্র। হিন্দুস্তানি ভাষার দাবিটি ছিল হিন্দি ভাষা প্রতিষ্ঠায় কৌশলগত অভিপ্রায় মাত্র। ওই কৌশলতাই অনিবার্য করে তোলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশভাগ।
লেখক: নির্বাহী সম্পাদক নতুন দিগন্ত
ভয়েস/আআ